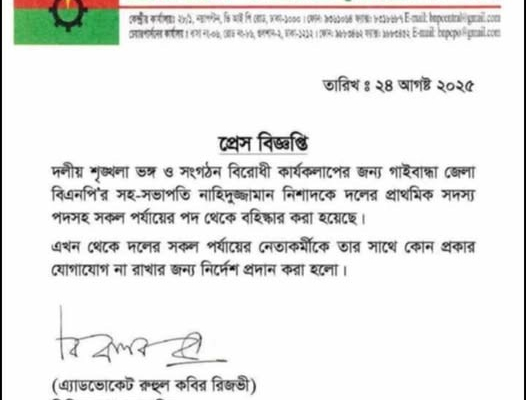পিআর পদ্ধতি কি? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুবিধা ও অসুবিধা

একরামুল ইসলাম তুষার,
সহকারী অধ্যাপক, ও কলামিস্ট।
PR অর্থ প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্ত্বিক নির্বাচন ব্যবস্থা । গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো জনগণের মতামতের যথাযথ প্রতিফলন। তবে অনেক সময় দেখা যায় প্রচলিত ভোট পদ্ধতিতে একটি দল সীমিত ভোট পেয়েও অধিকাংশ আসনে জয়ী হয়ে যায়, আর সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন দলকে সুষম হারে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট কীভাবে প্রদান করা হয়েছে তা প্রতিফলিত হয়। অধিক ভোট পাওয়া দলের কোনো আসনই থাকে না। এমন বৈষম্য থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে বিশ্বের বহু দেশ গ্রহণ করেছে প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (PR) বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা।
পিআরপদ্ধতিতে রাজনৈতিক দল বা জোট যে পরিমাণ ভোট পায়, তার আনুপাতিক হারে সংসদে আসন পায়। ফলে ছোট ছোট দলও আসন পায় এবং তাদের গুরুত্ব বাড়ে।গড়ে ওঠে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায্য প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ।
পিআর পদ্ধতি কী?
আনুপাতিক নির্বাচনী ব্যবস্থা হলো এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে ভোটারদের রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলগুলোর ভোট প্রাপ্তির হার অনুযায়ী। ভোটারা ভোট দেয় একটি দলকে ব্যক্তিকে নয়। কোনো দল যদি ৪০% ভোট পায়, তাহলে সংসদে তাদের আসনও হবে প্রায় ৪০% হারে।
বাংলাদেশসহ আরও অনেক দেশে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে যে দল বেশি আসনে জয় পায় তারা সরকার গঠন করে, ভোটের মোট শতাংশ নয়।
বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায়, একটি দল ৪২% ভোট পেয়ে আসন পেল ১৯৫ টি। আরএকটি দল ৪০% ভোট পেয়ে আসন পেল ৬০টি।
পিআর পদ্ধতিতে দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব আরও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। কিন্তু এলাকা ভিত্তিক দলীয় প্রার্থীর গুরুত্ব কমে যায়।
উদাহরণ স্বরূপ : পাঁচটি দল একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। একজন প্রার্থী ৩০% ভোট পেলেও বাকিরা মিলে ৭০% ভোট পেলেও, প্রচলিত পদ্ধতিতে সেই ৩০% প্রার্থীই জয়ী হবে। অর্থাৎ ৭০% ভোটের কোনো কার্যকর প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। পিআর পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন করেন, ১৮৯৯ সালে বেলজিয়ামে । বর্তমানে বিশ্বের ১৭০টি গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ৯১টি, পিআর ভিত্তিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উন্নত দেশের ৩৬টি দেশের মধ্যে ২৫টি, দেশ পিআর পদ্ধতি অনুসরণ করে।
পিআর পদ্ধতির ধরণ-
১. মুক্ত তালিকা পদ্ধতি: দলগুলো ভোটের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে থেকে আসন পায়।
২.বদ্ধ তালিকা পদ্ধতি: দল ঠিক করে দেয় কে হবেন সংসদ সদস্য।
৩.মিশ্র পদ্ধতি: কিছু আসনে প্রতীকভিত্তিক, কিছু আসনে পিআর ভিত্তিতে নির্বাচন হয়।
রূপ কার্যকর রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—
জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে, স্পেন, গ্রিস, ইতালি।এশিয়া: ইসরাইল, নেপাল, শ্রীলংকা।আফ্রিকা: দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, অ্যাঙ্গোলা।লাতিন আমেরিকা: ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, উরুগুয়ে।ওশেনিয়া: নিউজিল্যান্ড।তবে বিভিন্ন দেশে এর প্রয়োগও ভিন্ন। যেমন—জার্মানিতে মিশ্র পদ্ধতি রয়েছে, যেখানে ভোটাররা একদিকে সরাসরি প্রার্থীকে ভোট দেন, আবার দলকেও ভোট দেন। সংসদে আসন বণ্টন হয় এ দুটি হিসাব মিলিয়ে। অন্যদিকে ইসরাইল পুরোপুরি পিআরভিত্তিক নির্বাচন পরিচালনা করে, যেখানে কোনো সংসদ সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হন না—বরং দলীয় তালিকা থেকে আসন পূরণ করা হয়।
পিআর পদ্ধতির সুবিধ-
১. ছোট দল ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সংসদে প্রবেশের সুযোগ পায়।
২. ভোটের সঠিক প্রতিফল জনগণের দেওয়া ভোটের শতকরা হার আসনে প্রতিফলিত হয়, ফলে ভোটের অপচয় কমে।
৩. সংসদে নানা মতাদর্শের সহাবস্থান ঘটে, যা গণতন্ত্রকে বহুমাত্রিক করে।
৪. প্রতিটি ভোটের মূল্য আছে বলে মানুষ ভোট দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত হয়।
পিআর পদ্ধতির অসুবিধা
১. সাধারণত কোনো একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না, ফলে বারবার জোট সরকার গঠন করতে হয়। এছাড়া দলগুলোর মধ্যে মতের মিল না হলে সবসময় সরকার ভেঙে যাওয়ার একটি আশঙ্কা থাকে।
২. সংসদে কম সংখ্যক আসন থাকা দলগুলোও সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা অনেক সময় জটিলতা তৈরি হয়।
৩. নানা মতাদর্শের কারণে সংসদে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে কোন আইন প্রণয়ন করতেও দীর্ঘ সময় লেগে যায় বা অনেক সময় তা সম্ভব-ই হয় না।
৪. সরাসরি ভোটে নির্বাচিত এমপির মতো জনগণের সঙ্গে এমপিদের সম্পর্ক সবসময় ভালো থাকে না। এলাকার চেয়ে দলের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা বেশি দেখা যায়।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পিআর বিতর্ক-
বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যমান ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতিতে সর্বাধিক ভোট পাওয়া প্রার্থীই বিজয়ী হন। তবে রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরে সমালোচনা রয়েছে যে এই ব্যবস্থায় প্রকৃত ভোটের প্রতিফলন ঘটে না। যেমন—কোনো প্রার্থী ৩৫ শতাংশ ভোট পেলেও বিজয়ী হতে পারেন, আর বাকি ৬৫ শতাংশ ভোট কার্যত ‘অকার্যকর হয়ে পড়ে।
এ কারণে জামায়াতসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল দাবি তুলেছে, বাংলাদেশে আংশিক বা পূর্ণ পিআর ব্যবস্থা চালু করা হোক। তাদের যুক্তি, এতে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সঠিক প্রতিফলন ঘটবে এবং ভোটাররা তাদের ভোটের পূর্ণ মূল্য পাবেন। তবে বড় দলগুলো মনে করছে, এতে স্থিতিশীল সরকার গঠন ঝুঁকির মুখে পড়বে।
‘পিআর,’ পদ্ধতিতে অনেক সময় ছোট দলগুলো সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। যেমন – ইতালি এটার বাস্তব উদাহরণ। কোয়ালিশন সরকারেও এমন পরিস্থিতি দেখা যায়।
বাংলাদেশে ‘পিআর’ পদ্ধতির চ্যালেঞ্জ-
বিশ্বের যেসব দেশে পিআর ব্যবস্থা চালু সেসব দেশে গণতন্ত্রের বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি বেড়েছে। তবে এর সঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ঘনঘন জোট পরিবর্তনের যেমন – ইসরাইল ও নেপালে প্রায়ই সরকার পরিবর্তন হয়, কারণ কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। অপরদিকে, জার্মানি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, কারণ সেখানে মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমে ভারসাম্য আনা হয়েছে।
বাংলাদেশে যদি পিআর পদ্ধতি চালু হয়, তবে কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা হবে, পুরোপুরি নাকি আংশিক মিশ্র ব্যবস্থায়, তা নিয়ে বড় ধরনের বিতর্ক দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছ।
‘বাংলাদেশ পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের জন্য এখনো প্রস্তুত নয় বলে অনেক মনে করেন। কারণ বাংলাদেশের রাজনীতির মান এখনো উন্নত নয়। পিআর পদ্ধতিতে দল ঠিক করবে কে এমপি হবে। সেক্ষেত্রে আগে যে ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে দলীয় মনোনয়ন কিনতো, সে তখন ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনবে। দলও বলবে আপনি আমাকে ৫০ লক্ষ কোটি টাকা দেন আপনাকে মনোনয়ন দেবো।
প্রকৃত রাজনীতিবীদেরা পিআর পদ্ধতিতে মূল্যায়িত হবেন না বলে মনে করেন অনেকে। পুরাতন ‘রাজনৈতিক ধারায় যারা রাজনীতি করেন যাদের জীবন-মরণ ঐ রাজনীতি তখন ঐ লোকগুলো আর মূল্যায়িত হয় না। কারণ তাদের তো আর এতো টাকা পয়সা নাই।
এই পদ্ধতি ভোট দেওয়ার প্রতি ভোটার আনাগ্রহও তৈরি হবে বলেও মনে করেন এই , ‘পিআর পদ্ধতিতে প্রার্থী নির্বাচন করে দল। ভোটারদের তাদের নিজেদের প্রার্থী বাছাই করে নেওয়ার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে ভোটারদের মধ্যে ভোট দিতে অনাগ্রহ তৈরি হতে পারে।’
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুমাত্রিক করার সুযোগ দেয়। তবে এর সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বড় চ্যালেঞ্জ। বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা বলছে, প্রতিটি দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পদ্ধতিটি কার্যকর বা অকার্যকর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের জন্যও এ বিতর্ক হয়তো নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার দ্বার খুলতে পারে, আবার অস্থিরতার ঝুঁকিও বয়ে আনতে পারে।